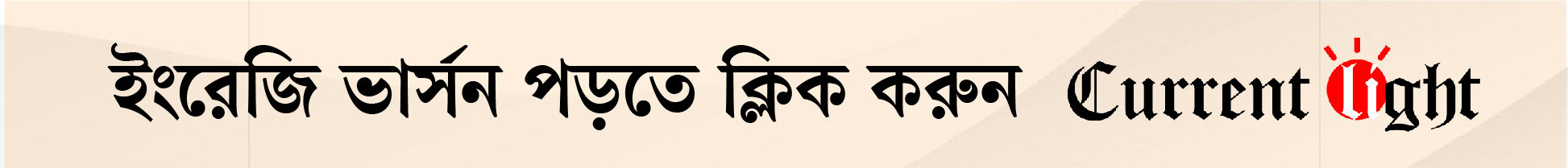রাজশাহীর বুকে যখন রৌদ্রঝলসা আষাঢ় মাসের সূর্য নেমে আসে মাথার ঠিক ওপরে, তখন ধানখেতে জল থাকে না, পুকুরে জমে থাকা কাদার স্তর হাঁটু ছুঁয়েই থেমে যায়, আর কৃষকের চোখে খেলে যায় এক বিষণ্ন তৃষ্ণার ছায়া। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ—পদ্মা, যমুনা, মেঘনা ও শত নদী-নালায় গড়া এই ভূখণ্ড দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত ছিল উর্বরতার প্রতীক হিসেবে। অথচ সেই দেশেরই উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বরেন্দ্র অঞ্চল যেন হয়ে উঠেছে এক নিঃশব্দ অভ্যন্তরীণ মরুভূমি, যেখানে পানির জন্য হাহাকার প্রতিদিনের বাস্তবতা।
খরা এখানে নতুন কিছু নয়, এটি বরেন্দ্রের ইতিহাসে দীর্ঘদিনের সঙ্গী। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ায় এই খরার চরিত্র আরও হিংস্র, আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টি হয় না, বর্ষার পানির বদলে আকাশ থেকে নামে ঝাঁঝালো তাপ, আর ফাটল ধরে জমির বুকে—ঠিক যেন সেখানে জীবনের নয়, মৃত্যুর বীজ বপন হচ্ছে। কৃষকরা আজ আর আগের মতো মৌসুমের উপর নির্ভর করে চাষ করতে পারছে না, কারণ বর্ষা আর শীতের ছন্দে যে নিয়মিতা ছিল কৃষির ক্যালেন্ডার, সেটি এখন এলোমেলো। একসময় বরেন্দ্রের মাটিতে দেশি ধান স্বাভাবিকভাবে ফলত, এখন তার বীজ পর্যন্ত শুকিয়ে যায় মাটির গর্ভে জল না পেয়ে।
গভীর নলকূপ কিংবা সেচ প্রকল্পের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে, অথচ পানির স্তর ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে, যা কৃষির টেকসই ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে। এই সংকট শুধু কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত এক জটিল সংকটে পরিণত হয়েছে। পানি নেই, তাই মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তরুণেরা শহরমুখো হচ্ছে, নারীরা সংগ্রাম করছে প্রতিদিনের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন নিয়ে। বরেন্দ্র জনপদ যেন আজ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের এক ভাঙা আয়না—যেখানে প্রতিফলিত হয় জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম সত্য। অথচ এই সত্যকে আমরা এখনো নীতিনির্ধারক পর্যায়ে পুরোপুরি গুরুত্ব দিচ্ছি না। খরা আর বরেন্দ্র যেন আর কেবল ভৌগোলিক বাস্তবতা নয়, এটি হয়ে উঠেছে এক রাজনৈতিক নীরবতা ও অবহেলার প্রতীক।
এই জনপদের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব কৌশল ও জ্ঞান দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে এসেছে—জমিতে চাষাবাদের পদ্ধতি বদলেছে, দেশি ধান, পাট ও ডাল জাতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে—তবু আজ তাদের পক্ষে আর টিকে থাকা সহজ নয়। তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞাননির্ভর, জনকেন্দ্রিক এবং জলবায়ু-সচেতন একটি পরিকল্পনা, যা শুধু বরেন্দ্রকে নয়, সমগ্র দেশকে প্রস্তুত করতে পারে আগামীর এক অনিশ্চিত জলবায়ু বাস্তবতার জন্য।
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব বরেন্দ্রে বহুগুণ বেশি প্রকট। মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে অনেক সময় তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁই ছুঁই করে। এই গরম শুধু মানুষের দেহকে পুড়িয়ে দেয় না, মাটির ভেতরের প্রাণশক্তিকেও শুষে নেয়। শস্য জন্মাতে গেলে প্রয়োজন নির্দিষ্ট আর্দ্রতা ও উষ্ণতা; কিন্তু বরেন্দ্রে সেটি আর পাওয়া যাচ্ছে না। এতে করে বাড়ছে ফসলের ব্যর্থতা, মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং কৃষি খাতে অনিশ্চয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সেচনির্ভর চাষাবাদের জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষকই এখন গভীর নলকূপের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে পানি উত্তোলনের খরচ এতটাই বেড়েছে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষে তা বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজেল ও বিদ্যুৎচালিত পাম্প, পাইপলাইন স্থাপন, শ্রমিকের মজুরি—সব মিলিয়ে এক বিঘা জমিতে সেচ দিতে খরচ পড়ছে পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।
এই চরম বাস্তবতার নির্মম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার নিমঘটু গ্রামের ঘটনা। ২০২২ সালের ২৩ মার্চ সেখানকার দুই সাঁওতাল কৃষক—অভিনাথ মারান্ডি ও তাঁর চাচাতো ভাই রবি মারান্ডি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। তাঁদের পরিবারের ভাষ্যমতে, স্থানীয় একটি গভীর নলকূপ অপারেটর ১২ দিন ধরে পানি সরবরাহ না করায় বোরো ধানের খেত শুকিয়ে ফেটে যায়। চোখের সামনে সারা বছরের স্বপ্ন ধ্বংস হতে দেখে হতাশা ও ক্ষোভে তাঁরা আত্মহননের পথ বেছে নেন। এই ঘটনা শুধু একটি পরিবার নয়, বরেন্দ্র জনপদের অগণিত প্রান্তিক কৃষকের নিঃশব্দ আর্তনাদের প্রতীক হয়ে আছে।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফলন হ্রাসের করুণ বাস্তবতা। ধান, গম, আলু, ডাল—সব খানেই ক্ষতি। একটি মৌসুম পার করেই কৃষক ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন। কেউ জমি বন্ধক রাখছেন, কেউবা চাষ ছাড়ছেন। এক অদৃশ্য ঋণের দুষ্টচক্রে আটকা পড়ে কৃষিজীবীরা পরিণত হচ্ছেন শহরমুখী অভিবাসীতে।
এই পরিস্থিতির মধ্যে আশার কথা হতে পারত কৃষিতে অভিযোজন কৌশল। কিন্তু সেখানেও বড় রকমের ঘাটতি আছে। এখনো অধিকাংশ কৃষক পানি-নির্ভর উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের উপর নির্ভর করছেন, যেখানে প্রয়োজন ছিল খরা সহিষ্ণু দেশীয় জাত ছড়িয়ে দেওয়া।
একসময় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে ধানের মাঠ মানেই ছিল দেশীয় জাতের সুশোভিত বিস্তার—গোবিন্দভোগ, জামাইভোগ, মোগাইবালাম, রূপকথা, শনি, পরাঙ্গী, কালামানিক, কালাবকরী, রাঁধুনীপাগল কিংবা পাঙ্গাসের মতো জাতগুলো শুধু ফসল নয়, ছিল গ্রামীণ জীবনের আবেগ ও ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। এই জাতের ধানগুলো অপেক্ষাকৃত কম পানিতে ভালো ফলন দিত এবং খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য ছিল আদর্শ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব জাত এখন হারিয়ে যাচ্ছে। হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল ধানের আগ্রাসনে দেশীয় ধানগুলো পেছনে পড়ে গেছে—আর সেই সঙ্গে বদলে গেছে চাষাবাদের খরচের কাঠামো ও কৃষকের জীবনধারা।
এখন হাইব্রিড জাতের ধান চাষে কৃষকদের বেশি সেচ দিতে হয়, ফলে সেচ খরচ বেড়েছে উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, যা একদিকে পরিবেশ দূষণ করছে, অন্যদিকে কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে কয়েকগুণ। যে ভূগর্ভস্থ পানি আগে শস্যচক্রে সঞ্চিত থাকত, আজ তা অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে। পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাওয়ায় ভবিষ্যতে সেচনির্ভর এই কৃষি ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
অথচ কৃষকেরা স্মরণ করেন সেই সময়, যখন দেশি ধান চাষের ব্যয় ছিল কম, জমির স্বাস্থ্যের ক্ষয় ছিল না, আর ধান কাটার পর গ্রামে বইত উৎসবের হাওয়া। নতুন ধান উঠলে তৈরি হতো চিড়া, খই, মুড়ি, পিঠা-পায়েস—অন্ন আর আনন্দের সেই দিন আজ কেবল স্মৃতিতে। ইতোমধ্যে হারিয়ে যাওয়া বা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাওয়া দেশি ধানের তালিকায় উঠে এসেছে: দুমড়া, চাপালো, কাচাননী, ধলকাচাই, গড়িয়া, মৌমাইল, জশোয়া, নীলকমর, নয়ারাজ, বসি, বেতো, পানিশাইল, শাইল্যা, বেগুনবিচি ইত্যাদি। এই ধানগুলো শুধু একটি কৃষি পদ্ধতির নাম ছিল না, ছিল একটি সংস্কৃতির অংশ, যা আজ হারানোর পথে। এখন প্রশ্ন উঠেছে—আমরা কি শুধুই উৎপাদনের সংখ্যাতত্ত্ব দেখব, নাকি খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবেশ, সংস্কৃতি ও কৃষকের অস্তিত্বকেও গুরুত্ব দেব?
অবস্থার জটিলতা শুধু কৃষিতেই সীমাবদ্ধ নয়। খরার ফলে পানির সঙ্কটে পড়েছে মানুষ ও গবাদিপশু। গ্রামীণ নারীদের দৈনন্দিন জীবনে এর চরম প্রভাব পড়ে—তাদের দিনে দুই-তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পানি আনতে হয়। স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে, সময় অপচয় হয়, আর শিক্ষা বা আয়মুখী কাজে তাদের অংশগ্রহণ কমে যায়। শিশুরা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, আর পুরো পরিবার অনিশ্চয়তায় জীবনযাপন করছে।
সরকারি পর্যায়ে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা প্রশংসনীয় হলেও অনেক সময়ই প্রযুক্তিনির্ভর ও খণ্ডিত প্রকৃতির। গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে অনেক, খাল খননের উদ্যোগও হয়েছে। কিন্তু এগুলোর বেশির ভাগই স্থায়ী রূপ নেয়নি। ভূগর্ভস্থ পানির পুনঃভরণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং স্থানীয় খাল-জলাশয় সংরক্ষণের মতো উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল বৃহত্তর পরিসরে। তদুপরি বরেন্দ্র অঞ্চলকে জলবায়ু পরিবর্তনের ‘ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল’ হিসেবে বিশেষায়িত করে একটি সমন্বিত অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমে দরকার স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা—যেখানে কৃষক, নারী, যুবক ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিকে কৃষকের কাছে সহজ করে পৌঁছানো এবং পরিবেশবান্ধব চাষপদ্ধতি যেমন মালচিং, ড্রিপ ইরিগেশন এবং ‘সিস্টেম অব রাইস ইন্টেনসিফিকেশন (SRI)’ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি। তৃতীয়ত, সামাজিক অভিযোজনের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকা, নারীর পানি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ এবং স্কুলভিত্তিক জলবায়ু শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে।
বরেন্দ্র আজ এক সংকটপুঞ্জের নাম। এই সংকটকে শুধুই কৃষি বা খরার পরিভাষায় ব্যাখ্যা করলে আমরা ভুল করব। এটি একটি সার্বিক পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো আমাদের উন্নয়ন-ভবিষ্যতের ছায়াছবি বহন করছে। বরেন্দ্রর ভবিষ্যৎ আমাদের সকলের দায়িত্ব। নীতিনির্ধারকদের উচিত, এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু-সহিষ্ণু নীতিমালা প্রণয়ন, যেখানে কৃষি, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবিকার প্রশ্নে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা যুক্ত হবে।
আমরা যদি এখনই বরেন্দ্রর প্রতি ন্যায্য নজর না দিই—তবে অদূর ভবিষ্যতে এটি হয়ে উঠবে দেশের প্রথম পরিবেশগত ধ্বংসস্তূপ। সেই দায় শুধু প্রকৃতির না, তা হবে আমাদের নির্বিকার নীরবতার প্রতিচ্ছবি।
লেখক: সৈয়দ নাভিদ আনজুম হাসান
তরুণ গবেষক ও জলবায়ু কর্মী